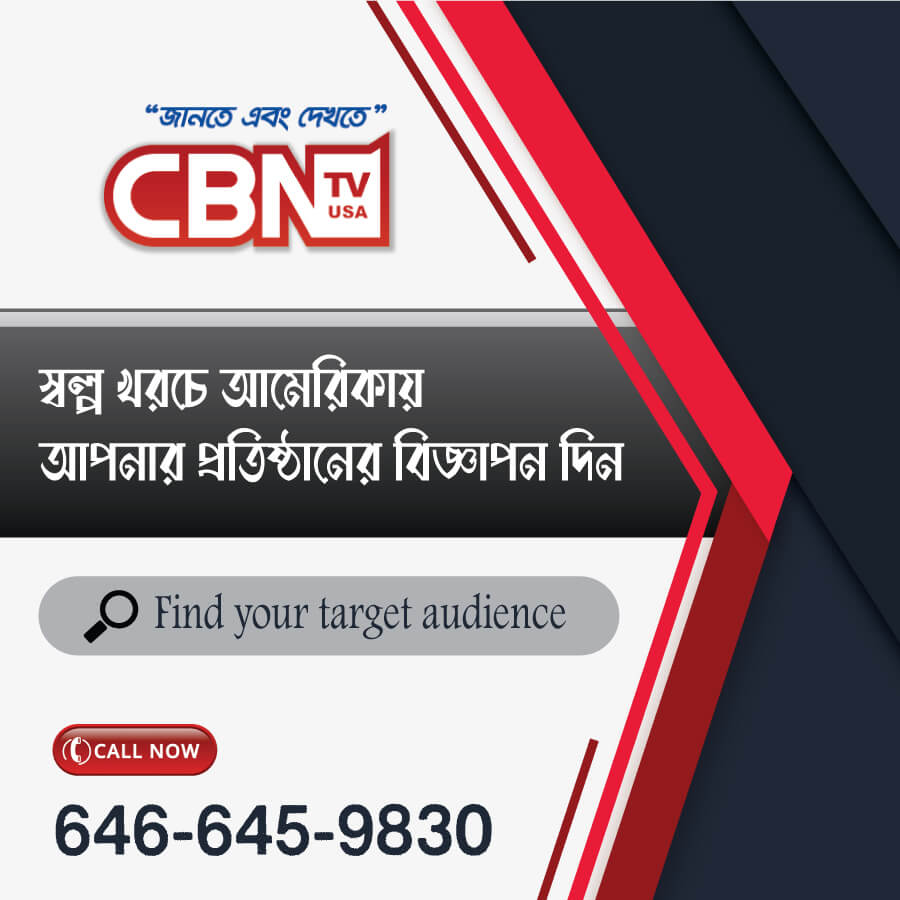আফতাব চৌধুরী: ভাষা হচ্ছে কতগুলো অর্থবহ ধ্বনি সমষ্টির বিধিবদ্ধ রূপ; যার সাহায্যে একটি বিশেষ সমাজের লোকেরা নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময় করে। যে জনসমষ্টি এক ধরনের ধ্বনি সমষ্টির বিধিবদ্ধ রূপের দ্বারা নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময় করে ভাষা বিজ্ঞানীরা তাকে একটি ভাষা সম্প্রদায় হিসেবে আখ্যায়িত করেন। এখানে একটি ধ্বনি সমষ্টির উল্লেখ করা যাক- ‘আমরা বই পড়ি’। এ ধ্বনি সমষ্টি নির্দিষ্টক্রমে বিন্যস্ত করে শুধু বাঙ্গালিরা ব্যবহার করে এবং এর দ্বারা যে ভাব প্রকাশিত হয় তা আমরা বাঙ্গালিদের একটি ভাষা-সম্প্রদায় হিসেবে অভিহিত করতে পারি।
এ ক্ষেত্রে ইংরেজরা যে ধ্বনি সমষ্টি ব্যবহার করবে তা হল- উই রিড বুকস। জার্মানরা এ ক্ষেত্রে বলবে- উইর লেসেন বিলসার। ফরাসিরা বলবে- নুয়াস লিসন্স ডেসলিভার্স। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে, একই ধরনের ধ্বনি সমষ্টি দিয়ে সব মানুষের কাজ চলে না। এক এক ধরণের ধ্বনি সমষ্টি ও ধ্বনি সমাবেশ-বিধিতে এক একটি জনগোষ্ঠী অভ্যস্ত।
ভাষা হচ্ছে মানুষের এমন এক অনন্য সুলভ বৈশিষ্ট্য, যা অন্য প্রাণী থেকে মানুষকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে, তার স্বাতন্ত্রের এ অভিজ্ঞানটি সে পৃথিবীতে তার আবির্ভাবের পর ক্রমবিকাশের ধারায় অর্জন করছে। এ অনন্য সুলভ সম্পদটি শুধু তার আছে। কারণ তার প্রয়োজন আছে এ সম্পদের। তার কারণটি অবশ্য আমরা যদি তলিয়ে দেখি তবে দেখতে পাব এর মূলে আছে আবার অন্য একটি আরো গভীরতম মানব বৈশিষ্ট্য, যেটি অন্য প্রাণীর নেই। সেটি হচ্ছে মানুষের মন এবং মনের ক্রিয়াজাত তার চিন্তারাজি। বিবর্তনের ধারায় ঝড়ের পরে প্রাণের বিকাশ হওয়ায় বৃক্ষলতা-পশুপক্ষীর আবির্ভাব সম্ভব হয়েছে। এর পরের ধাপে মনের বিকাশের ফলে মানুষের আবির্ভাব হল।
মন আছে বলে মানুষ চিন্তা সম্পদের অধিকারী। নিজের ভাব ও চিন্তার সম্পদকে অন্যের কাছে পৌঁছে দিতে চায় বলে তার প্রয়োজন হয় এক উন্নততর প্রকাশ মাধ্যম যার নাম ‘ভাষা’। শুধু ক্ষুধা-তৃষ্ণা বা অন্য জৈববৃত্তি প্রকাশের তাগিদে ভাষার জন্ম হয়নি। জৈব চাহিদাকে অন্যের মনে সঞ্চার করে সমস্যার সহজতর সমাধানে ভাষা আমাদের সহায়তা করে ঠিক কিন্তু পুরোপুরি জৈব বৃত্তির তাগিদে ভাষার জন্ম হয়নি।
যদি শুধু জৈব তাগিদে ভাষার জন্ম হত, তবে জীবজন্তুরা ভাষার জন্ম দিতে পারত অথবা শুধু জৈব প্রয়োজন মিটাতে হলে জীবজন্তুর মতো অস্ফুট ভাষা ও ইঙ্গিত হলে মানুষের কাজ হয়ে যেত। বস্তুর উন্নততর ভাব ও চিন্তাকে প্রকাশের জন্য মানুষের ভাষার প্রয়োজন। এ জন্য চিন্তা ও ভাষার মধ্যে অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক রয়েছে। চিন্তার সঙ্গে, মানুষের মনের সঙ্গে তার আত্মার সঙ্গে ভাষার এ অপরিহার্য সম্পর্ক আছে বলে জার্মান মনিষী হুমবোল্ট আরো গভীরে গিয়ে বলেছেন- মানুষের ভাষা হল তার আত্মা, আর আত্মা হল তার ভাষা।
উক্তিটিতে কবি সুলভ উচ্ছ্বাস আছে স্বীকার করি। কিন্তু অস্বীকার করতে পারি না যে, মনীষীর মূল অনুভূতিটি নির্ভূল কারণ ভাষার সঙ্গে মানুষের মন ও তার আত্মার যোগ অবিচ্ছেদ্য। অর্থাৎ ভাষার উৎস তার মনে, মনের চিন্তারাজির প্রকাশের তাগিদে ভাষার জন্ম। ভাষা হচ্ছে মানুষের চিন্তার ধ্বনি মাধ্যম বিকাশ। ভাষাবিদরা বলেছেন, চিন্তা ও ভাষা মূলত এক, পার্থক্য শুধু এটুকু যে চিন্তা হল নিজের সঙ্গে নিজের নীরব কথোপকথন এবং যে প্রবাহটি আমাদের চিন্তা থেকে ধ্বনির আশ্রয়ে ওষ্ঠের মধ্য দিয়ে বয়ে আসে তা হল ভাষা।
ভাষা সৃষ্টির মূলে মানুষের দুটি দিক রয়েছে। ব্যক্তি মানুষের মন ও চিন্তা, সমাজবদ্ধ মানুষের ভাব বিনিময়ের ইচ্ছা। অর্থাৎ ভাষার যেমন একটি ভাবগত উৎস আছে, তেমনি একটি সমাজগত চাহিদাও আছে।
আধুনিককালে সাহিত্যের যেমন সমাজগত দিকটি বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হচ্ছে, তেমনি ভাষার সমাজগত দিক প্রাথমিক তাৎপর্য লাভ করছে। ভাষা বিজ্ঞানীরা তাই প্রথমে মনে করিয়ে দিচ্ছেন- ‘দ্যা ফার্স্ট পয়েন্ট উই মাস্ট মেক এবাউট ল্যাঙ্গুয়েজ, দেন, ইজ দ্যাট ইট ইজ এ সোস্যাল, র্যাদার দেন এ বায়োলজিকেল অ্যাসপেক্ট অফ হিউম্যান লাইফ।’ তাই ভাষা বিজ্ঞানীরা আজকাল সমস্বরে বলছেন, ‘ভাষা হচ্ছে একটি সামাজিক সংস্থা।
এ কথার তাৎপর্য দ্বিবিধ। প্রথমত, ভাষার জন্ম সামাজিক প্রয়োজনে অর্থাৎ সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ভাব বিনিময়ের প্রয়োজনে। দ্বিতীয়ত, ভাষার প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হয় সমাজের কাঠামো অনুসারে। যে সমাজে শিশুর প্রতি সম্পর্কের আচরণের পার্থক্য আছে, সেখানে তাদের প্রত্যেকের জন্য ভাষার রয়েছে পৃথক পৃথক নাম-সম্পর্ক চিহ্ন। তাছাড়া কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সামাজিক গঠনের পরিবর্তন ঘটছে। ফলে এ সব সম্পর্ক চিহ্নের পরিবর্তন ঘটছে। সামাজিক প্রয়োজনে ও সামাজিক কাঠামো ভাষার প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। এসব কারণে আমরা ভাষাকে একটি সামাজিক সংস্থা বলতে পারি।
আমাদের সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, সভ্যতার ক্রমবিকাশের দ্বারা যেমন ক্রমোন্নতি লাভ করবে তেমনি তার নতুন নতুন নান্দনিক উপলব্ধি, সূক্ষ্ণাতিসূক্ষ্ণ ভাব ও বৈজ্ঞানিক আবিস্ক্রিয়া প্রকাশের জন্য ভাষাকে হতে হবে তত সূক্ষ্ণ উন্নত ও মার্জিত প্রকাশক্ষম।
লেখক: সাংবাদিক ও কলামিস্ট।